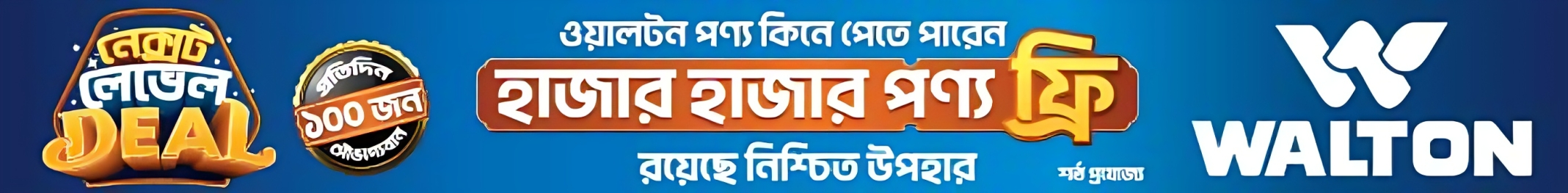সময় সমাচার ডেস্ক :
‘তারিখ-ই-ইলাহী’ ক্যালেন্ডারের প্রচলন-পরবর্তী ফসল কাটা হলে কৃষকরা কর পরিশোধ করেন। পরের বছরও তাই করেন। সৌর বছর হিসাব করার ফলে আগের মতো নওরোজ বা বছরের সূচনা দিন সরে এল না। এতে অর্থবছর এবং ফসলের আগমনের ফারাক ঘুচে গেল। ফলে কৃষকদের কাছে এটা ‘ফসলি সন’ বলে পরিচিত হয়। বাংলার সুবাদাররা ফসলি সন হিসেবেই কর আদায় শুরু করলে মোগল আমলে বাংলায় এটি সরকারি ক্যালেন্ডার হিসেবে মর্যাদা পায়। কৃষকের এবং শাসনের সুবিধার্থে প্রচলন করা হয় সন গণনার এ রীতি। আকবরের পর ‘তারিখ-ই-ইলাহী’ টিকে না থাকলেও বঙ্গাব্দ টিকে আছে এখনো।
প্রতি বছরই পহেলা বৈশাখ এলে দিনটি নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়। পহেলা বৈশাখ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কিনা তা নিয়েই এ তর্ক। বিষয়টি অবশ্যই সাংস্কৃতিক, তবে সেই সঙ্গে আবার অনেকটাই সামাজিক। সমাজে নানা সময়ে নানা মতের দিকে ঝোঁকে মানুষ। একটা সময়ের জনগোষ্ঠীর এক অংশের মনে হয়েছিল পহেলা বৈশাখ তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এখন কারো কারো মনে হচ্ছে, দিবসটিকে ঘিরে পালিত হওয়া অনেক আয়োজন আসলে ‘বাঙালি’ সংস্কৃতির অংশ নয়। ২০২৫ সালে এসে নতুন করে পহেলা বৈশাখকে পরিচয় করানো ও উদযাপনের একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। শোভাযাত্রার নাম বদলে দেয়া হলো। কিন্তু এই সবকিছুর আড়ালে আরেকটা আলাপের বিষয় থাকে—বাংলা সনের সূচনা।
প্রতিটি দেশ ও ভাষাভাষী মানুষের কাছে তাদের নিজেদের বর্ষপঞ্জি, তারিখ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা নিজেদের নতুন বছর আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করে। বাংলা সনের ক্ষেত্রে সেখানে আরেকটি তর্ক আসে, বঙ্গাব্দ চালু হওয়া নিয়ে।
বঙ্গাব্দের সঙ্গে অনেকে মিল পান শকাব্দের। সেই সঙ্গে বিক্রম সংবৎকেও টানা হয়। কিন্তু আদতে বাংলা সন চালু হয়েছিল মোগল আমলে, বাদশাহ আকবরের হাত ধরে। আকবর নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার করেছিলেন। চালু করেছিলেন নতুন কিছু নিয়ম। এর অনেকগুলোর পেছনেই ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। বাংলা সন চালুর পেছনেও ছিল মোগল শাসনের সুবিধা নিশ্চিত করার ইচ্ছা। সেই সঙ্গে তিনি অবশ্য কৃষকের কথাও কিছুটা ভেবেছিলেন। সে কারণেই তারিখ গণনার এ ব্যবস্থা ও বাংলা বর্ষপঞ্জির নাম হয়েছিল ‘ফসলি সন’।
মোগল শাসন থেকে কোষাগারে মোট যে খাজনা আসত তার একটি বড় অংশের উৎস ছিল বাংলা। অবশ্য তা জাহাঙ্গীরের সময়ের পর থেকে। কেননা বাংলায় মোগল শাসন সুসংহত হয়েছিল তারই শাসনামলে। তবে আকবরের আমলেও খাজনা খুব একটা কম যেত না। কেননা ফসলের অভাব ছিল না বাংলায়। এর বাইরে ছিল আরো নানা শিল্প। তাই বাংলা নিয়ে আলাদা করে ভেবেছিলেন আকবর। প্রয়োজনটা ছিল তার নিজের। আরো স্পষ্ট করে বললে, মোগল সাম্রাজ্যের। বাংলা থেকে খাজনা নিতে কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছিল।
আকবর খেয়াল করেছিলেন বাংলার জীবন ও রীতিনীতি উত্তর ভারতের মতো নয়। নদীবিধৌত বাংলার মাটি উর্বরা। প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চলের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। ফসলের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন, জীবিকা, উৎসব। আকবর খেয়াল করে দেখেন যে, ফসল ওঠার মৌসুমেই বাংলার মানুষের উৎসব। তাহলে সে সময়েই খাজনা নেয়া ভালো। এছাড়া সেই হিসাব রাখার জন্য আলাদা একটি সন গণনা করতে পারলে তো আরো ভালো হয়।
আকবরের আদেশ অনুসারে তার সভাসদ ও জ্যোতিষী, আমির ফতেউল্লাহ সিরাজি বছর গণনার এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ হিসাবে আকবরের সিংহাসন আরোহরের দিনকে আদিবিন্দু ধরে সন গণনা শুরু হয়। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে দাপ্তরিকভাবে চালু হয় এ সন। আকবর সিংহাসন আরোহণ করেন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। সেই হিসাবে আকবরের রাজত্বের ২৯তম বর্ষে এ সন গণনা শুরু হয়। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের সময়কে প্রথম বছর ধরার কারণে সন চালু হয় ২৯তম বছর থেকে। এ নতুন সনের নাম দেয়া হয় ‘তারিখ-ই-ইলাহী’। আকবরের প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে এ নতুন সনের নামের মিল রয়েছে।
আকবরের দাপ্তরিক কাজে সাধারণত হিজরি ও ইলাহী, দুই সনই আলাদা করে লেখা হতো। অনেক পণ্ডিতের ধারণা, বাংলায় তখন শকাব্দের ব্যবহার ছিল। আকবরের দপ্তরে যে হিসাব থাকুক না কেন, বাংলার জন্য তৈরি হলো অন্য প্রথা। সেখানে হিজরি সনের সঙ্গে সমন্বয় করে বছরের হিসাব তৈরি হলো। আকবর ৯৬৩ হিজরি, ১০ রবিউল আউয়াল, শুক্রবার অনুসারে ১৪৭৯ শকাব্দ ও ইংরেজি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যেহেতু ওই বছর হিজরি ৯৬৩ সাল ছিল, তাই ওই সালটিকে ৯৬৩ বঙ্গাব্দ ধরে সন গণনা শুরু করা হয়। অর্থাৎ বাংলা সন শুরু হয়েছে ৯৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে। ৯৬৩ হিজরির ১ মহরমকে ১ বৈশাখ ৯৬৩ বঙ্গাব্দ হিসেবে সন গণনা করা হয়।
এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, হিজরি মাস গণনা এবং বাংলা মাস গণনার রীতি ভিন্ন। হিজরি বছর এবং মাস গণনা হয় চন্দ্রের হিসেবে, অর্থাৎ হিজরি বছর চান্দ্র। কিন্তু বাংলা বছর, মাস গণনা করা হয় সূর্যের আবর্তন অনুসারে। অর্থাৎ বাংলা বছর সৌর বছর এবং হিজরি বছরের সঙ্গে এর যোগাযোগ কেবল বছর গণনার সুবিধার্থে, সূচনা নির্ধারণে।
হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্মতভাবে নক্ষত্রের নামে ফতেউল্লাহ সিরাজী ১২ মাসের নাম রাখেন—
১. বিশাখা থেকে বৈশাখ; সূর্য তখন মেষ রাশিতে অবস্থান করে।
২. জ্যেষ্ঠা থেকে জৈষ্ঠ; সূর্যের অবস্থান বৃষ রাশিতে।
৩. উত্তরাষাঢ়া থেকে আষাঢ়; মিথুন রাশিতে সূর্য অবস্থান করে।
৪. শ্রাবণা থেকে শ্রাবণ; সূর্যের অবস্থান কর্কট রাশিতে
৫. পূর্বভাদ্রপাদ থেকে ভাদ্র; সূর্যের অবস্থান সিংহ রাশিতে।
৬. আশ্বিনী থেকে আশ্বিন; কন্যা রাশিতে সূর্য অবস্থান করে।
৭. কৃতিকা থেকে কার্তিক; সূর্য তখন তুলা রাশিতে।
৮. মৃগশিরা থেকে অগ্রহায়ণ; বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য অবস্থান করে।
৯. পুস্যা থেকে পৌষ; সূর্যের অবস্থান ধনু রাশিতে।
১০. মঘা থেকে মাঘ; মকর রাশিতে সূর্যের অবস্থান।
১১. উত্তরফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন; কুম্ভ রাশিতে সূর্য অবস্থান করে এবং
১২. চিত্রা থেকে চৈত্র; সূর্যের অবস্থান মীন রাশিতে।
‘তারিখ-ই-ইলাহী’ ক্যালেন্ডারের প্রচলন-পরবর্তী ফসল কাটা হলে কৃষকরা কর পরিশোধ করেন। পরের বছরও তাই করেন। সৌর বছর হিসাব করার ফলে আগের মতো নওরোজ বা বছরের সূচনা দিন সরে এল না। এতে অর্থবছর এবং ফসলের আগমনের ফারাক ঘুচে গেল। ফলে কৃষকদের কাছে এটা ‘ফসলি সন’ বলে পরিচিত হয়। বাংলার সুবাদাররা ফসলি সন হিসেবেই কর আদায় শুরু করলে মোগল আমলে বাংলায় এটি সরকারি ক্যালেন্ডার হিসেবে মর্যাদা পায়। কৃষকের এবং শাসনের সুবিধার্থে প্রচলন করা হয় সন গণনার এ রীতি। আকবরের পর ‘তারিখ-ই-ইলাহী’ টিকে না থাকলেও বঙ্গাব্দ টিকে আছে এখনো।
তবে আকবর যে বাংলা সন প্রবর্তন করেছেন সে কথা অনেকে স্বীকার করতে নারাজ। বাংলা সনের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আকবরের আমলে চালু হওয়া বর্ষপঞ্জির কথাই বলা হয় কিন্তু একালে এসে অনেকে ভিন্ন যুক্তি দেন। তাদের কারো মতে, আকবর বাংলা সন চালু করেননি, করেছিলেন ইলাহী সন। আবার কেউ বলে থাকেন বাংলা সন চালু করেছিলেন শশাঙ্ক। কিন্তু শশাঙ্কের বাংলা সনের খুব একটা ব্যবহার কোথাও দেখা যায় না। সে তুলনায় শকাব্দ ব্যবহৃত হতো বেশি। ১০০-১৫০ বছর আগে ছাপা হওয়া বইয়েও শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।
বাংলা সন নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে কেউ বলে থাকেন ফতেউল্লাহ সিরাজি নতুন কিছু করেননি, এগুলো আগেই ছিল। কিন্তু কথা হলো, সেটা থাকলেও বিষয়টি তিনি সংস্কার করে বৃহত্তর ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছিলেন। শশাঙ্কের বর্ষপঞ্জি, শকাব্দ বা বিক্রম সংবৎ থেকেও যদি বাংলা সন এসে থাকে তা পরিণত হয়েছিল মোগল শাসক আকবরের দরবার থেকেই।
মাহমুদুর রহমান: লেখক, মোগলনামা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)